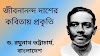আমাদের
ইতিহাসে এমনসব নির্মম সত্য লুকিয়ে আছে যা আমাদের অনেকেরই জানা নেই। সেসব কথা ভাবলে
আজও আমাদের মন ঘৃণায় ভরে ওঠে, লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসে। যেমন পৃথিবীর ইতিহাসে
আমেরিকাতে একবার একটি হাতিকে নির্মমভাবে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। এ ঘটনাটি যেমন বিরল
ঠিক তেমনি এ ঘটনাটিও সত্যি যে একসময় মানুষদের বন্দীকরে পশুরমত খাঁচায় রাখা হত এবং
বহু মানুষ টিকিট কেটে সেসব রক্ত-মাংসের মানুষদের দেখতে যেত। জানি এ ঘটনা অনেকেরই বিশ্বাস
করতে কষ্ট হবে। কিন্তু অবিশ্বাস্য মনে হলেও ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহন করছে। সত্যিকার
অর্থেই আমাদের এই পৃথিবীতে একসময় মানুষের চিড়িয়াখানা ছিল। আমাদের স্বাভাবিক ধারণায়
চিড়িয়াখানায় শুধুমাত্র জন্তু-জানোয়ার থাকে এবং এদের প্রদর্শনী হয়, কিন্তু তা বলে
রক্ত-মাংসের জ্যান্ত মানুষের প্রদর্শনী? ঘটনাগুলো ঘটেছিল আঠারোশ শতকের দিকে। ইউরোপ-আমেরিকার
বড় শহরগুলোতে সাদা চামড়ার অভিজাত মানুষের তীব্র জাতিবিদ্বেষের শিকার হয়ে কালো
মানুষরা পরিণত হয়েছিল প্রদর্শনীর বস্তুতে। বর্তমান যুগের চিড়িয়াখানাগুলোতে যেভাবে
জালদিয়ে এবং খাঁচা তৈরি করে পশুদের আটকে রেখে প্রদর্শনী করা হয়, তখন কালো মানুষদের
এভাবে প্রদর্শন করা হতো। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গা থেকে সাদা চামড়ার মানুষ
তাদের দেখতে আসত।
আমরা ইতিহাস খুঁজলে দেখতে পাবো, এই ঘটনাগুলো খুব বেশি পুরনো নয়। এগুলো ১৮০০ শতাব্দীর শেষ থেকে ১৯০০ শতাব্দী জুড়ে দেখা যেত। গোটা পৃথিবীতে তখন জাতিগত বিদ্বেষ চরমে পৌঁছেছিল। সাদা চামড়ার মানুষদের হাতে প্রায়ই নির্যাতিত ও নিগৃহীত হত কালো চামড়ার মানুষেরা। সমাজের সবচেয়ে নিচু কাজগুলো করতে তাদের বাধ্য করা হত। দাস হিসেবে সাদা চামড়ার মানুষদের নির্যাতন সহ্য করতে করতেই কেটে যেত জীবনের বাকি বছরগুলো। নিজস্ব জীবনের স্বপ্ন দেখার সময়ও তারা পেত না। তারও অনেক পরে বর্ণবাদ প্রথার বিলুপ্তির মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখল।
বিভিন্ন বই
পড়ে এবং ইতিহাস থেকে জানা গেছে মাত্র ২০০ বছর আগে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে তৈরি
হয়েছিল ‘মানব চিড়িয়াখানা’। ইতিহাস মুছে ফেলা যায়না বলেই হয়তো আজ আমরা সেসব ঘটনা
জানতে পারি ও ভেবে আঁতকে উঠি। কখনও তাদের খাঁচায় বন্দী করে রাখা হত আবার কখনও
প্রাকৃতিক পরিবেশে বন্দীকরে অ-ইউরোপীয়, আফ্রিকান, এশিয়ান এবং আদিবাসী মানুষদের
দেখানো হতো। বিশেষভাবে কালো চামড়ার মানুষেরাই ছিল এই প্রদর্শনীগুলোর প্রধান
আকর্ষণ।
পাঠকদের
অবগতির জন্য জানাই, এইসব অমানবিক চিড়িয়াখানাগুলো দেখা যেত প্যারিস, হামবুর্গ,
জার্মানি, বেলজিয়াম, স্পেন, লন্ডন, বার্সেলোনা, মিলান, পোল্যান্ড, সেন্ট-লুইস,
নিউইয়র্ক ইত্যাদি শহরে। মনে করা হয় এই কাজে সাদা মানুষেরা দারুণ আনন্দও পেত কারণ
না হলে তারা খরচ করে ওই খাঁচায় বন্দী মানুষগুলোকে দেখতে যেত না বা মানব
চিড়িয়াখানার ধারণা এত তাড়াতাড়ি প্রসার লাভও করতনা। বাণিজ্যিক ভাবেও এর আকর্ষণ
বেড়েছিল।
মানব চিড়িয়াখানাগুলোতে বহু প্রজাতির মানুষকেই রাখা হত, তবে এদের মধ্যে পিগমি প্রজাতির বেঁটে কালো কদাকার চেহারার ওটাবেঙ্গা সবচেয়ে বেশি আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। ওটা বেঙ্গার জন্ম হয় ১৮৮৩ সালে এবং মৃত্যু হয় ১৯১৬ সালের ২০শে মার্চ। ওটা বেঙ্গাকে আনা হয়েছিল সাউথ সেন্ট্রাল আফ্রিকার কঙ্গো থেকে। ওটাবেঙ্গাকে ১৯০৪ সালে সবার সামনে প্রথমবারের মত প্রদর্শন করা হয়। সেবার মিসৌরির সেন্ট লুইস-এ একটি জাতিগত লুইসিয়ানা রপ্তানি প্রদর্শনীতে ওটাবেঙ্গাকে দেখানো হয়। এর পর ১৯০৬ সালে ব্রোংস জু-এর বিতর্কিত মানব চিড়িয়াখানায় তাকে প্রদর্শন করা হয়। বেঙ্গা মূলত একজন আফ্রিকান দাস ছিলেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত অনেক প্রদর্শনীতে সেরা আকর্ষণ হিসেবে সাদা মানুষদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল ওটাবেঙ্গাকে। স্যামুয়েল ফিলিপ নামের একজন অভিযাত্রী তাকে মুক্ত করেন। ফিলিপ বিভিন্ন প্রদর্শনীর জন্য আফ্রিকান মানুষ সরবরাহের কাজ করতেন। বেঙ্গা ফিলিপের সঙ্গে আমেরিকা ভ্রমণও করেন। এর বাইরেও বেঙ্গা একাধিক প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন। বেঙ্গাকে যখন ব্রোংস জু-তে প্রদর্শিত করা হয়, তখন সবচেয়ে বেশি গণ্ডগোল ছড়িয়ে পরে চারিদিকে। বিতর্ক দেখা দেয় নানা সমাজে। সেখানে বেঙ্গাকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। তাকে জোর করে বাঁদরের মত লাফালাফি করতেও বাধ্য করা হত। এমনকি তাকে বাঁদরের খাঁচায় রেখে প্রদর্শন করা হয়। সকলের সামনে বেঙ্গাকে উপস্থাপনের আগে তার কোলে বাঁদর বা হনুমান প্রজাতির বাচ্চাকে তুলে দেওয়া হত এবং এরফলে পৃথিবীব্যাপী এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এর পর শেষজীবনটা বেঙ্গা আমেরিকার ভার্জিনিয়াতেই বসবাস করেছেন।
সবচেয়ে অদ্ভুত হল, প্রদর্শনীর সময় এদের জলচর প্রাণীর
মত জলের ভিতর রাখা হত আর সেখানে বিচিত্র ভঙ্গিতে লাফালাফি করতে বাধ্য করা হতো ।
শুধু তাই নয় কিছু কিছু প্রদর্শনীতেতো তাদের নগ্ন থাকতেও বাধ্য করা হত। সবচেয়ে
আশ্চর্যের বিষয় হল যাদের প্রদর্শিত করা হত তারাও যেমন মানুষ ছিল, যারা তাদের এই
ঘৃণ্য কাজ করতে বাধ্য করত তারাও মানুষই ছিল। এককথায় বলতে গেলে বলা যেতে পারে শ্রেণী-বৈষম্যের
চূড়ান্ত শিকার সেই মানুষগুলোকে জোরকরে আটকে রাখা হত। তাদের ইচ্ছা, অনিচ্ছার কোন
মূল্যই ছিল না। কেউ প্রতিবাদ করলে বা আপত্তি করলে তার ভাগ্যে জুটত নির্মম
নির্যাতন। এসব বন্দীদের বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ধরে আনা হত। তবে
এই ভয়ঙ্কর কাজটির সঙ্গে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাদা চামড়ার মানুষদের হাত ছিল বলে
জানা যায়। অবশ্য একথাও জানা যায় যে কেউ কেউ আবার অল্প কিছু মজুরির বিনিময়ে
প্রদর্শনীতে অংশ নিতে রাজি হয়ে যেত। তবে যথারীতি সেই মজুরির পরিমাণ ছিল
তুলনামূলকভাবে অনেক কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের সঙ্গে খুব নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হত।
তাদের ঠিক মত খাওয়ার বা থাকার ব্যবস্থাও ছিল না। তাদের সবসময়ে দাবিয়ে রাখার জন্যই
এরকম ব্যবহার করা হত। প্রদর্শনীর আয়োজকেরা জানত যে বন্দী মানুষটিকে যত বেশি
কিম্ভূত কিমাকার দেখতে হবে তাকে দিয়েই তত বেশি আয় করা সম্ভব হবে। টিকিট বেশি
বিক্রি হবে তাকে দেখতে। তাই বন্দীদের দেখাশোনার কোনও প্রয়োজনীয়তাই তারা বোধ করতেন
না উদ্যোক্তারা বা মালিকেরা। এর ফলে দেখা যেত প্রদর্শনীতে ঢোকার কিছুদিনের মধ্যেই
কালো মানুষেরা অধিকাংশই অসুস্থ হয়ে পড়তেন বা মারা যেতেন। তখন সেই শূন্যস্থান
পূরণের জন্য নতুন কাউকে তুলে আনা হত বা ভাড়া করে আনা হত। পাঠকেরা শুনলে আরও অবাক
হবেন যে ১৮৩৩ সালের এক আন্তর্জাতিক ঔপনিবেশিক মানুষ রপ্তানি প্রদর্শনীতে সুরিনামের
স্থানীয় মানুষদের প্রদর্শন করা হয়। সেটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল আমস্টারডামে।
কিছু কিছু প্রদর্শনীতে বেশি লাভের
আশায় কালো চামড়ার নারীদের প্রদর্শনীতে নগ্নভাবে উপস্থাপন করা হত। এতে টিকিট
বিক্রিও বেশি হত। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানাযায়, ১৯৩১ সালে পার্সিয়ান আন্তর্জাতিক
মানব চিড়িয়াখানার এক প্রদর্শনীতে ৬ মাসে প্রায় ৩৪ মিলিয়ন লোকের সমাগম ঘটেছিল। মাঝে
মাঝে আশ্চর্য লাগে এই ভেবে যে আজও কি আমরা এর থেকে খুব বেশি দূরে সরে আসতে পেরেছি?
আমাদের চিন্তাধারার সত্যিই কি কোনও আমূল পরিবর্তন হয়েছে?
আমরা চিড়িয়াখানায় গেলে বাঁদর বা হনুমানের খাঁচার সামনে গিয়ে যেমন ব্যবহার করি, আগেকার সাদা মানুষগুলোও কিন্তু প্রায় সকলেই ওই কালো মানুষগুলোর সঙ্গে পশুর মত ব্যবহার করত। সে সময়ে মানব চিড়িয়াখানার ধারণাটি অভিনব এবং দর্শনার্থীদের বিপুল চাহিদার কারণে এটি খুব তাড়াতাড়ি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া এটি সেসময় এক লাভদায়ী ব্যবসা হিসেবে দেখা দিয়েছিল। তাই এই প্রদর্শনীগুলোর চাহিদাও বেড়ে গিয়েছিল প্রচুর পরিমাণে। এর চাহিদা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এর চর্চা শুরু হয়ে যায় এবং অভিজাত সাদা চামড়ার মানুষের পাশাপাশি অনেক বড় ব্যবসায়ীও এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই ব্যবসা শুরু করে দেন। কোনও কোনও প্রদর্শনী দল সার্কাস দলের মত বিশ্বের বড় বড় শহরগুলোতে তাদের প্রদর্শনী নিয়ে ভ্রমণ শুর করে। একে প্রদর্শনী না বলে ভ্রাম্যমান চিড়িয়াখানা বলাই ঠিক হবে। প্রচুর মানুষ দলে দলে দেখতে আসত এইসব কালো মানুষদের। এসব প্রদর্শনীর সাফল্যও ছিল ঈর্ষণীয়। উদ্যোক্তারা তখন থেকেই কালো মানুষের সঙ্গে এধরনের আচরণের বিষয়টিকে জাতিগত প্রদর্শনী বলে চালিয়ে দিত।
জানা যায়, ১৮৭৪ সালে কার্ল হ্যাগেনব্যাক নামের একজন জার্মান
ব্যবসায়ী স্যামন (Samoan
) এবং
সামি (Sami)
নামের
প্রজাতির মানুষদের নিয়ে একটি প্রদর্শনী করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কার্ল হ্যাগেনব্যাক
ছিলেন একজন বন্যপ্রাণী সরবরাহকারী এবং ইউরোপের বিভিন্ন চিড়িয়াখানার উদ্যোক্তা
ব্যবসায়ী। সে সময় এই প্রদর্শনীটির নাম দেওয়া হয়েছিল ‘পিউরলি ন্যাচারাল’ এবং এই
প্রদর্শনীটি সাদা মানুষদের মধ্যে দারুণ সাড়া জাগিয়েছিল। হ্যাগেনব্যাক ১৮৭৬ সালে তার
একজন সহযোগীকে পাঠিয়েছিলেন মিশরের সুদানে। সেখান থেকে কিছু বন্য পশু এবং নুবিয়ান
আদিবাসীদের নিয়ে আসার জন্য। এই নুবিয়ান অধিবাসীদের নিয়ে হ্যাগেনব্যাকের প্রদর্শনী
সাফল্য লাভ করে। এই নুবিয়ান আদিবাসীদের নিয়ে তিনি যে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন তা
ইউরোপ থেকে শুরু করে প্যারিস, লন্ডন এবং বার্লিনেও প্রদর্শিত হয়। এর পর থেকে শুরু
হয়ে যায় কালো মানুষদের নিয়ে প্রদর্শনীর রমরমা ব্যবসা। ১৮৭৭ সালে প্যারিসের একটি
উদ্যানের তৎকালীন পরিচালক ছিলেন জিওফ্রে ডি সেইন্ট হিলারি। তিনি সিদ্ধান্ত
নিয়েছিলেন তার প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে নুবিয়ান এবং ইনুইট মানুষদের নিয়ে দুটি
প্রদর্শনী আয়োজন করার। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল সে বছর সেই উদ্যানের দর্শনার্থীর
সংখ্যা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে উদ্যোক্তাদের উৎসাহ আরও বেড়ে
যায়। চলতে থাকে প্রদর্শনীর রমরমা ব্যবসা।
এরপর ১৮৭৭ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত কমপক্ষে তিরিশটি আলাদা আলাদা এ ধরনের
প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন উদ্যানের পরিচালকেরা। প্রতিটি প্রদর্শনীতেই বিপন্নপ্রায়
আদিবাসী কালো চামড়ার মানুষেরা প্রদর্শনীর বস্তুতে পরিণত হয়।
পার্সিয়ান বিশ্বমেলা অনুষ্ঠিত হয় ১৮৭৮ এবং ১৮৮৯ সালে এবং
সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হল সেখানেও অন্যতম আকর্ষণ ছিল এ ধরণের প্রদর্শনী। জানা গেছে
১৮৭৮ সালে নাইজার (Negre ) নামে একটি গ্রামকে তুলে ধরা হয়েছিল প্রদর্শনীতে এবং সেবার
মেলায় ২৮ মিলিয়ন লোকের সমাগম হয়েছিল। আর ১৮৮৯ সালে প্রায় ৪০০ আদিবাসী মানুষকে নিয়ে
এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল।
খুব বেশি দিনের কথা নয়, ১৯৯০ সালে বিশ্বমেলায় মাদাগাস্কারের বিখ্যাত ডিয়রামার প্রদর্শনী করা হয়। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক প্রদর্শনী মার্সেলিস (১৯০৬ এবং ১৯২২), ঔপনিবেশিক প্রদর্শনী প্যারিস (১৯০৭ এবং ১৯৩১) সেখানেও খাঁচার মধ্যে মানুষদের বন্দী করে প্রদর্শন করা হয়। এসব মানুষের কেউ কেউ অর্ধনগ্ন আবার কেউ কেউ একেবারেই বস্ত্রহীন ছিল।
শুধুমাত্র আফ্রিকানরাই নয়। বিভিন্ন দেশের আদিবাসীদের এভাবে খাঁচায়
বন্দী করে প্রদর্শনীতে রাখা হত। জানা গেছে ইশি নামে এক আমেরিকান আদিবাসীকেও এভাবে
বন্দী করে খাঁচায় রেখে প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল। তাই বর্তমানের তথাকথিত সভ্য
মানুষদের থেকে আমরা এটুকুতো আশা করতেই পারি যে ভবিষ্যতে এধরনের ঘটনার আর
পুনরাবৃত্তি হবে না।
লেখকের অন্যান্য লেখা পড়তে এখানে ক্লিক করুন ।
কালীপদ চক্রবর্ত্তী দিল্লি থেকে প্রায় ১৮ বছর ‘মাতৃমন্দির সংবাদ’ নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন এবং ‘সৃষ্টি সাহিত্য আসর’ পরিচালনা করেছেন । বর্তমানে 'কলমের সাত রঙ' এবং 'www.tatkhanik.com' পত্রিকার সম্পাদক।
দিল্লি,কলকাতা এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখেন। কলকাতার আনন্দমেলা, আনন্দবাজার পত্রিকা,সাপ্তাহিক বর্তমান, কথা সাহিত্য, দৈনিক বর্তমান, নবকল্লোল,শুকতারা, শিলাদিত্য,সুখবর, গৃহশোভা, কিশোর ভারতী, চিরসবুজ লেখা (শিশু কিশোর আকাদেমী,পশ্চিমবঙ্গ সরকার), সন্দেশ, প্রসাদ, ছোটদের প্রসাদ, কলেজস্ট্রীট, উল্টোরথ,তথ্যকেন্দ্র, জাগ্রত বিবেক (দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির থেকে প্রকাশিত) , স্টেটসম্যান, কিশোর বার্তা , অন্যান্য বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রকাশিত বই-এর সংখ্যা ১০ টি এবং প্রকাশের পথে ২টি বই।

.jpg)
.gif)