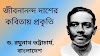পটভূমি
এই সময়টাকে শিষ্ট সমাজের (ব্রাহ্মণ্য ও সামন্ত)
অবিমৃশ্যকারিতার যুগ বলা যায়। পুরোপুরি বিজাতীয় ইসলাম ধর্মাবলম্বী শক্তির কাছে
অত্যন্ত রক্ষণশীল সেনরাজশক্তি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হল। যারা বাঁচল তারা পদানত হয়ে
নিজেদের স্বার্থ বাঁচাতে ব্যস্ত রইল, প্রজাদের কথা ভাবল না। অন্যদিকে বাঙালি
শিষ্ট সমাজ এই ঘোর বিপদ থেকে বাঁচার তাগিদেও সর্ববর্গকে সাথে নিয়ে থাকতে পারল না।
জাতপাত, অস্পৃশ্যতা, নারী নিপীড়ন,
নিম্নবর্গের মানুষদের শোষণ বেগার প্রথায় ও বিপদে আপদে ছলনার দাদন
দিয়ে বা দয়া দেখিয়ে, ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও সামন্তবর্গ বৃহত্তর
হিন্দু সমাজকে দুর্বল, নিঃস্ব, উদ্যমহীন
করল। তাদের উপর আস্থা যতটুকু ছিল তাও হারালো। তবু বৃহত্তর হিন্দু সমাজ ফাঁদে পড়ে
দুই দিক থেকেই পদদলিত ও শোষিত হয়েও পরম্পরাকে ধরে রইল। বেশ কিছু সংখ্যক নিরাপত্তা
ও কিছুটা আত্মসম্মান পেল ধর্মান্তরে। আর শিষ্ট সমাজ আরও বেশি সংকুচিত হল ধর্মের
নামে কুসংস্কার অভ্যাস করিয়ে সুনামের বদলে দুর্নাম মাথায় মুখে মেখে নিজেদের
বাঁচালেন। তারা সমৃদ্ধ হলেন রাজশক্তির চাটুকার বা তোষামুদে পার্শ্বচর হয়ে আবার কখনও
ঘরের মেয়ে ও বাল্যবিধবাদের কাশী-বৃন্দাবনের নামে মূল্য ধরে দিয়ে।
সাহিত্যেও, যেহেতু ধর্ম ও রাজ্যবর্গের প্রশস্তি
মূলত:; ধ্বংস হল হিন্দু মন্দির, মঠ ও
টোল-পাঠশালা এবং বৌদ্ধ স্তূপ, বিহার ও বিদ্যালয়গুলির সাথে।
এই পরিস্থিতিতে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত বাংলা সাহিত্য অবহেলিত ও আহত
হতে থাকে। তবুও লোককথা লোকগানে ধরে নতুন দিনের আশায় রইল, কিছু
উচ্চবর্গের এবং সাধারণ মানুষরা। ছয় ঋতুর লোকাচারে ভুলতে চাইল ব্যথা। লোকভাষায়
সমবেত প্রার্থনা গান নাচ বন্ধ হল না বরং অরাজকতা অস্থিরতাতে সাধারণ মানুষ এগুলি
আরও আঁকড়ে ধরল। অল্প সংখ্যায় শিষ্ট মানুষও এই সুযোগ নিয়ে রচনা করলেন যাতে নবোপলীয়
ও তান্ন সভ্যতার কৃষ্টির প্রাধান্য স্পষ্ট। সাহিত্য এই ধারাতেই বইতে থাকল।
দ্ব্যর্থক ব্যঙ্গাত্মক ধর্মীয় ও সামাজিক চড়া কবিতা ও প্রবাদের প্রাদুর্ভাব দেখা
গেল। এই সময়টাকে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলা হয়। অনেকে তা মানেন না কারণ রমাই
পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ, খনার ও ডাটের বচন ও হলায়ুধ মিশ্রের 'সুপর্ণা' কবিতাগুচ্ছ অনেকটাই লোকসাহিত্যে প্রতিফলন
এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে আবার পরবর্তীকালে নতুন দিশা খুঁজতে
সাহায্য করেছে (সেন ১৯৭৯, বিশ্বাস ২০২০)।
পাল শাসনের শেষ অধ্যায় (১০০০-১১০০ খৃষ্টাব্দ)
ইতিহাস বলে পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম বিস্তার
লাভ করল সমস্ত বাঙলাতে আর হিন্দুধর্ম সংকুচিত হতে থাকল। কিন্তু ভারতে বিশেষ করে
বাঙলাতে ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের শেষদিকের বিবর্তনে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বৈদিক বিবরণ, ত্রিদেবগণ ও
সূর্য দেবতার কথা এবং পরিক্রমণের ব্যবহার এবং পৌরাণিক চার যুগের উল্লেখ দেখা যায়
যা মহাযান পন্থীদের ভাবধারণা বলে পরিচিত। বর্তমান ভারতে কোনও বৌদ্ধ তীর্থস্থানে এই
রকম বৈদিক-বৌদ্ধ ভাবধারার সমন্বয় না দেখা গেলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোনও দেশে
যেমন, থাইল্যান্ডের সংরক্ষিত সত্যের মন্দিরে স্পষ্ট
প্রতীয়মান। একভাগে পুরোব্রহ্মান্ড-ব্রণা, বিষ্ণুষ্ণু ও
মহেশ্বরের মূর্তি সহ, এক প্রবেশ দ্বারে হর-পার্বতী সপরিবারে
এবং আর এক প্রবেশ দ্বারে সূর্যদেবের মূর্তি (দাস ২০১৯)।
বাস্তবে বৌদ্ধধর্ম জন সাধারণের মধ্যে বেশি জায়গা করে নেয়
এবং তাদের মনে শক্ত হয়ে বসে ব্যতিক্রমী ভিক্ষু চর্যাপদ রচয়িতা ও গায়ক
সিদ্ধাচার্যদের প্রচেষ্টাতে। কিন্তু বখ্তেয়ারের আক্রমণে চর্যাপদ হারিয়ে গেল, সিদ্ধাচার্যরা
হলেন অজ্ঞাত। এদের অস্তিত্ব জানা গেল বিংশ শতাব্দীর গোঁড়ার দিকে। তবে শীর্ষ সমাজ
থেকে বৌদ্ধধর্ম ও পালি ভাষা নির্বাসিত হলেও জনসাধারণের, বিশেষ
করে নিম্ন বর্গের হিন্দুদের মধ্যে, কি করে টিকে রইল আরও কয়েক
শতাব্দী? পাল শাসনের শেষের দিকে রামাই পণ্ডিত নিয়ে এলেন আর
এক অভিনব ধর্ম ভাবনা ও অভ্যাস।
ধর্ম পূজা ও রামাই পণ্ডিত:
ব্রাহ্মণ্য সমাজের মধ্য দিয়ে ও পাল শাসেন নিযুক্ত
প্রভাবশালী সেন বংশীয়দের প্রোৎসাহে হিন্দু ধর্মও মাথা তুলতে থাকে। রামাই পণ্ডিতের
আবির্ভাব সেই সময়টায়। তিনি ভগবানকে অনুভব করলেন ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম
প্রচার মন্ত্রের তৃতীয় সূত্রে এবং তাঁকেই প্রধান বলে মানলেন। তাঁকে অবয়ব হীন মনে
করলেন। এটাও বৌদ্ধধর্ম-বোধির মূল ভিত্তি। কিন্তু বিহার ও উপাসনা ঘরের বদলে
হিন্দুদের মত মন্দিরে নিরাকার ধর্মঠাকুরের পূজার প্রবর্তন করলেন। মন্দির স্থাপনের
আগে বেশ কিছু দিন ছোট ছোট জনবসতিতে নিয়মিতভাবে চলতে থাকে এই অভ্যাস। ক্রমে ক্রমে
স্থানীয়দের আগ্রহে ও সক্রিয়তায় এমন কি তাদের অবদানে মন্দির গড়ে ওঠে। নিম্নবর্গের
মানুষরা, যারা হিন্দু সমাজে অতি গরিষ্ঠ, তারা বেশি প্রভাবিত হলেও বর্ধিষ্ণু কৃষক ও ছোট সামন্তবর্গও কম বেশি জড়িয়ে
পড়ে। ধীরে ধীরে এই অভ্যাস একটি সাধারণ রূপ নেয়- ধর্মঠাকুর ও ধর্মপূজার এবং তন্ত্র
সাধনার, মারণ উচ্চাটনের যজ্ঞের দেবী হারিতীদেবীর পূজাতে। ডোম,
পোদ, হাড়ি প্রভৃতি যারা ব্রাহ্মণ্য হিন্দু
ধর্মাভ্যাসে অস্পৃশ্য অচ্ছুৎ তারাই পূজারি ও ধর্মগুরু। উপকরণ, উপচার, রীতি আচার ইত্যাদিতে হিন্দু শাস্ত্রের মিশ্রণ
দেখা যায় যেমন, জলপাবন, টীকাপাবন,
অধিবাস, ধূনাজ্বালানো, সন্ধ্যাপাবন
ইত্যাদি। দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল পূজা পদ্ধতিতে চুনের ব্যবহার এবং
পূজারিগণের উপবীতের বদলে তাম্র ধারণ। পরে রামাই পণ্ডিতের রচিত শূন্য-পুরাণে এই
ধারণা ও অভ্যাস স্পষ্ট হয়। ব্যাখ্যা বিবরণে ও মন্ত্রতে মূর্তিহীনের প্রশস্তি,
মানবিকতার কথা এবং ভাষা, শব্দে ও বাক্যে,
সরলতায় বিশিষ্ট যেমন, "ভক্তানাং কামপূরং
সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্তিং।" শঙ্খ ধর্মের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়।
তন্ত্রমন্ত্রের প্রয়োগ শুরু হয় প্রতিপক্ষের উপর মারণ-উচ্চাটনের মধ্য দিয়ে। অনেক
পরে এই প্রথার উপর মঙ্গলকাব্যের রচনা হয় যা ধর্মমঙ্গল নামে পরিচিতি পায় তাতে
উল্লেখ আছে এগারোজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নাম যথা মাননাথ, গোরক্ষনাথ
প্রভৃতি। প্রাচীন রচনাগুলির উপর পরবর্তী কবি, গায়ক বা
সাহিত্যিকগণ অনুবাদ করতে গিয়ে নিজের ভাবনা চাপিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি। ধর্ম পূজার
আলোচনা করতে করতে সত্য ও দ্বাপর যুগে পৌঁছে গেছেন। আবার বলা হয়েছে পৌরাণিক চার
যুগে চার মূল পুরোহিত বংশ হলেন সত্যযুগে শেতাই ঠাকুরের, ত্রেতাতে
অস্পষ্ট, দ্বাপরে কংসাই পন্ডিত আর কলিতে রামাই পণ্ডিত এবং
ধর্মপূজার বিস্তার বোঝাতে গতি-সংখ্যার (থান বা মন্দিরের?) ব্যবহারে
বলা হয়েছে ৪০০, ১২০০ ও ১৬০০ যথাক্রমে (সেন ১৮৯৬, ১৯০১ ও ১৯০৮, দাস ২০১১)।
রামাই পণ্ডিতের জন্ম কখন তা স্পষ্ট নয়, যদিও দাবি করা
হয় এগারো শতাব্দীতে দ্বিতীয় মহীপালের সময়ে। তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারের, তাও নিশ্চিত হয়। বিয়ে করেন ৮০ বছর বয়সে ও এক ছেলের জন্ম দেন। তাঁর বংশধরগণ
এখনও বাঁকুড়া জেলার ময়নাপুর গ্রামের যাত্রা সিদ্ধি রায় (ধর্ম) ঠাকুর মন্দিরের পুরোহিত।
দেহান্ত হয় হাকন্দে-চাঁপাতলা ও ময়নাপুরের মাঝামাঝি। তবে তিনি যে শূণ্যপুরারের
রচয়িতা তা স্বীকৃত। নগেন্দ্র নাথ বসুর সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শূন্যপুরাণ
প্রকাশিত করে। এতে ৫১টি অধ্যায়, প্রথম পাঁচটি সৃষ্টি পত্তনের
উপর বাকি সব পূজা-পাবনের পদ্ধতির বর্ণনা যার কিছুটা আলোচিত হয়েছে পালরাজাদের
শাসনের শেষ থেকে সেন রাজাদের সময় কালে। তৎকালীন শব্দ ও ভাষার ব্যবহারের দরুণ এ
কালে বুঝতে অসুবিধা হলেও ছন্দ ও গীতিময়তা দৃষ্টি আকর্ষণ করে (সেন ১৮৯৬, ১৯০১ ও ১৯০৮), যেমন:
"যত দূর ধর্মের ওঁকার জান
গারস্তের মহাপাপ দুরস্ত পলান।"
"হে মধুসূদন বায় ভাই বার আদিও হতে পাতি লেহ সেবকর অর্থ পপ্পপানি সেবক হব
সুখী ধামাৎ করি গুরু পণ্ডিত দেওলা দান পাতি। মাংসুর ভোক্তা আমানি সন্ন্যাসী গতি
জইতি। গাএন বাএন দুআরি দুয়ারপাল ভাণ্ডারী। ভাণ্ডার পাল রাজদূত কোমি কোটাল পাব সুপ
মুরতি এডি দেউলে পড়িব জঅজআকার।”
টিকা: পুষ্প-পুর, প্রসন্ন-প্রসন্ন, শ্রীফল-ছিলফ, বজ্র-বজ্র ইত্যাদি-দেশজ ও সংস্কৃত বরং
প্রাকৃতে মিশ্রণ।
সেন রাজাদের সময়ের গোঁড়া হিন্দু শিষ্ট সমাজের
(ব্রাহ্মণ্য ও সামন্তবর্গ) কর্তাব্যক্তিগণ জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত শূণ্যপুরাণে
বর্ণিত বৌদ্ধ ধর্মকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতেন। তাঁরা ধর্ম পূজা, ধর্ম মন্দির,
ধর্ম ঠাকুর এবং অতি বড় সংখ্যার সংবেদনশীলদের ভিত ভাঙ্গতে ও মুছে
দিতে চাইলেও নিজেদেরকে কৌলীন্যের ও বিশুদ্ধতার নামে গণ্ডিরেখা টেনে আলাদা রেখেছেন।
অন্যদিকে রাজনীতি, প্রশাসন ও প্রতিরক্ষার বৃহত্তর স্বার্থের
কথা ভেবে রাজশক্তি প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ থেকে বিরত রয়েছেন। তাই দেখা যায় গুপ্তদের
সময়ে উদ্ভূত পশুবাদী শৈবরাই হিন্দু নবজাগরণের কারণে জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতায়
নামলেন সর্বব্যাপী বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিভূ ধর্ম পূজাকে মুছে দিতে।
নিম্ন বর্গের ব্যতিক্রমী বৌদ্ধ ধর্মবোধি-ধর্মগুরু এবং
ধর্মাভ্যাসের মন্দির ও শূণ্যপুরাণ-ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত পদ্ধতিকে স্থানীয় স্তরে
হিন্দুবোধি ও হিন্দু ধর্মাভ্যাস দিয়ে নতুন করে সাজিয়ে নেওয়াটা হল প্রথম কাজ। এতে
শিষ্ট সামন্ত-ব্রাহ্মণ্য সমাজের কোন ভূমিকা নাই। সেই নিম্ন বর্গের বৌদ্ধ ধর্মগুরুর
অনুচরগণই প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে হিন্দু শিব-গৌরী ও স্থানীয় দেবী-দেবদের বসিয়ে দিলে
আরাধ্য বৌদ্ধ ধর্মগুরুর আসনে সেই ধর্মমন্দিরগুলির অধিকাংশতে। সরে গেল শূণ্যপুরাণের
পদ্ধতি, চুনের বদলে চন্দ্রন ফিরে এল আর যজ্ঞোপবীত তাম্র কনকন কবচ মালার বদলে। প্রাচীন
বাঙলার পূজার উপকরণ - উপচার) গম্ভীর স্তব উচ্চারণ ও নীরবতা সরিয়ে দিয়ে সমবেত গীতি
বন্দনা ফিরিয়ে আনল আনন্দ মুখরতা। পরিবর্তিত ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির একটি সংকলিত রূপ
হল ঘনরামের শ্রীধর্মমঙ্গলকাব্য।
ধর্মগুরু প্রধানত হিন্দু দেবতা শিব, ধর্মমন্দিরগুলি
কয়েকটা ব্যতীত সবই স্থানীয় নামে পরিচিত পায়। আরাধনা ও পূজার জুড়ে গেল শিবের গাজন
কীর্তন ও স্থানীয় পূজনের রীতি আচারে। এই স্থানীয় মানুষদের ছড়া গীত বা সুরেলা কথনের
সঙ্গে নাচ আবশ্যিক হল (দীনেশ সেন ১৮৯৬, সুকুমার সেন ১৯৭৯ এবং
সুর ১৯৮৮, অনামা-ক ও খ ২০১৬)।
শুরু হল দীর্ঘ শ্রেণীদ্বন্দু-একদিকে শৈব ও স্থানীয়
দেবতাদের অনুগামীরা,
অন্যদিকে সামন্ত-ধর্মসমাজের প্রধানরা রঘুবীর জনার্দ্দনকে অর্থাৎ
বিষ্ণুকে নিয়ে। বাংলা সাহিত্যে এই ধর্মকলহ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব দিল নতুন রসদ তাতে
ভাযা ও লোকসাহিত্যের শ্রী ও বিস্তার দুইই বাড়ল। লোক সাহিতের আর একটি উৎস বহু
সংখ্যক ভ্রাম্যমান যোগী সাধুগণ। এঁনাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন দর্শনে মঙ্গলময়, বলনে নম্র, পরিবেশনে সরল ভাষা ও কৌতুক প্রিয়তাতে
আকর্ষণীয়। পান্ডিত্য অগাধ কিন্তু প্রকাশ সংক্ষেপে দিনলিপির সাধারণ কথায়, উপমায় তাই সহজে বোধগম্য। গ্রামে গ্রামে পুরুষ নারীরা ঘিরে বসে তাঁদের কথা
শুনতে। বুদ্ধিজীবী ও উচ্চবর্গের নজরে তাঁদের এই ছোট ছোট আসরগুলি গাঁজাখোরের
প্রতিপত্তি বা অজ্ঞলোকের বিশ্বাস, ইত্যাদি। কিন্তু পল্লী কবি
ও গীতিকাররা সেখানে দেখেন তাদের জীবন দর্শনের গুঢ় তত্ত্ব ও বাস্তবতার মিল। তাঁদের
বলা কওয়াতে বিষ্ণু শিবের বিরোধিতা নেই, বরং আছে সখ্যতা আর
বেদের এক ঈশ্বরের বহু প্রকাশের গল্প। এর ফলে সাধারণ মানুষের মনে হিন্দু-বৌদ্ধের
বিদ্বেষ ভাবনাটা প্রশমিত করার ইচ্ছা জাগে। শূন্য পুরাণের ধর্মমঙ্গলগুলিকে যে ভাবে
বদলে নিজেদের ধর্মমঙ্গল করেছে তাতে একদা পূজা বৌদ্ধ ভিক্ষু ও স্থানীয় শ্রদ্ধাভাজন সংশ্লিষ্ট
মানুষদের কথা থাকেনি। সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্য সেই দিক থেকে ভিন্ন। এখানে
হর-পার্বতীর বিয়ের বর্ণনার সাথে সেই সব বৌদ্ধ সাধুদের কথাও রয়েছে (সেন ১৮৯৬,
১৯০১ ও ১৯০৮)। তাঁর রচনাও দেশজ ও সংস্কৃত শব্দের মিশ্রণে, থান ও বৈদিক ভাবে সমৃদ্ধ তেমনি অনুপ্রাস ও অনুরণনের সংযত প্রয়োগে মধুর-
"শরণ লৈনু, জগজ্জননী, ও রাঙ্গা
চরণে তোর।
ভব
জলধিতে, অনুকূল হৈতে, কে আর আছয়ে মোর।। হরিহর ব্রহ্মা,
যে পদ পূজয়ে, তাহে কি বলিব আমি। বিপদ সাগরে,
তনয় ফুকারে, বুঝিয়া যা কর তুমি।।"
শূণ্য পুরাণও হিন্দু জাগরণের আগে ও পরে অক্ষত থাকেনি।
রামাই পণ্ডিত নিজে জগন্নাথ রূপী বিষ্ণুকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। পরে শঙ্খ বিষ্ণু
বন্দনাতে সমৃদ্ধ হয় আর শিবের মঙ্গলময় রূপ আদৃত হয় বন্দনায়। আরও পরে সৈয়েদ
বদিরুদ্দিনের মাদারিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের ভাব ধারায় রচিত একটি অধ্যায় নিরঞ্জনের
রুস্না। এই অধ্যায়ে হিন্দু দেব দেবীদের মুসলমান নাম দেয়া হয়। কিন্তু তারা রুষ্ট হয়
যখন দক্ষিণা বা ভিক্ষা না পেয়ে, মন্দির বাড়ি ধ্বংস করে যা বর্ণনাতে
রয়েছে-(সেন ১৮৯৬, ১৯০১ ও ১৯০৮)।
"দেউল দেহারা ভাঙ্গে ক্যাড়্যা কাড়্যি
খায় রঙ্গে
পাখর পাখর বলে বোল।
ধরিয়া ধর্মের পায় রামাঞ্চি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিসম গণ্ডগোল।"
কোন মুসলমান উপদ্রব উপলক্ষ করে এই অধ্যায় রচিত তা স্পষ্ট
নয়। তবে এটা রামাই পণ্ডিতের নিজের রচনা নয়, তার কারণ বখতেয়ারের আক্রমণের
সময়ে তাঁর জীবিত থাকার সম্ভাবনা খুব কম।
ধর্ম পূজা, শূন্যপুরাণ ও ভিক্ষুদের লিখিত ধর্মমঙ্গল
কাব্যগুলিও এক মিশ্রিত বৌদ্ধ-বৈদিক বোধি ও অভ্যাসের রূপ। ইতিহাস এই পর্যন্ত কবি বা
সাহিত্যিকগণ ধর্ম কলহ ও ধর্মীয় শ্রেণীষন্দু সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন।
তথ্যসূত্র:
১) অতুল সুর: ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়: প্রবন্ধ-ভারতের
আবায়বিক নৃতত্ত্ব,
ভাষার যাদুঘর, গ্রামীণ সমাজ ও জীবন চর্যা এবং
প্রাগৈতিহাসিক প্রেক্ষাপট-সাহিত্য লোক, কলকাতা,, ১৯৯৮।
২) দীনেশ চন্দ্র দাস থাইল্যান্ড এবং বৌদ্ধ-বৈদিক ই
সমন্বিত ধর্ম ও বোধ। মাতৃমন্দির সংবাদ, উনবিংশ বর্ষ, ৭২তম
(শারদ) সংখ্যা, দিল্লি, ২০১৯, পৃঃ ৩৯-৪৪।
৩) দীনেশ চন্দ্র দাস: রাজশক্তি সমাজ ও ধর্ম অনুশাসনের
পেষণে বাংলা সাহিত্য-প্রাসঙ্গিকতা। ফিরে দেখা মাসিক, সপ্তবিংশতি
বর্ষ, দশম ও একাদশ সংখ্যা, কলকাতা,
২০২০, পৃঃ ৭-৮।
৪) দীনেশ চন্দ্র দাস: বঙ্গভাষা ইতিহাসে প্রেক্ষাপটে।
উন্মুক্ত উচ্ছ্বাস ত্রিভাষিক সাহিত্য পত্রিকা, ত্রৈমাসিক,
ষড়বিংশ বর্ষ, বইমেলা সংখ্যা, দিল্লি, ২০২১, পৃঃ ৯৮-১০৭।
৫) দীনেশ চন্দ্র সেন: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ইন্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ এবং
ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কলকাতা, ১৮৯৬ ১ম, ১৯০১-২য় ও ৩য় ১৯০৮ সংস্করণ।
৬) Anonymous (অনামা ক): The Development of
Bengali Literature during Muslim rule and Sufi Literature. Retrieved from
Archieves, Banglapedia, 2016.
৭) Anonymous (অনামা খ) Bengali Literature
under Islamic Rule, Wickipedia and Banglapedia, 2016.
৮) Sukumar Sen: History of Bengali, Sahity
Akademi, New Delhi, 1979.
লেখকের অন্যান্য লেখা পড়তে এখানে ক্লিক করুন।
লেখক পরিচিতি –
স্কুল-কলেজ পেরিয়ে উচ্চশিক্ষা পান আই টি খরগপুর, নেডারল্যান্ডস্ ও জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ইউ এস এ -তে । কর্মক্ষেত্র উত্তর প্রদেশ-এর তরাই অঞ্চলের গ্রাম, ভারত সরকার-এর অধীনে অরুণাচল-এ, (শিলং-এ থেকে), উটি (তামিলনাড়ু), দেরাদুন-এ (উত্তরাখণ্ড) , কৃষি এবং পরিবেশ মন্ত্রালয়, দিল্লি-তে।
দিল্লির ৩৪ পল্লীর কালীবাড়ির সাথে যুক্ত আছেন বিগত ৩০ বছর ধরে। ১৯৪৮ সাল থেকেই লেখেন কিন্তু প্রথম প্রকাশন ২০১৫-তে। কবিতা , গল্প, ভ্রমণ কাহিনী ও প্রবন্ধ ছাপতে থাকে দিল্লির পত্র-পত্রিকাগুলোতে। কলকাতা এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। প্রথম বই ' অনুভূতি বহুরূপে'। অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে দিল্লিথেকে প্রকাশিত ম্যাগাজিন ' কলমের সাথ রঙ' পত্রিকার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং উচ্চপদে আছেন।

%20%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B6%20%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%20%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B8.jpg)