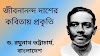রবীন্দ্রনাথ -
নজরুল –
পারস্পরিক
সম্পর্কের কথকতা
ড. বাসুদেব রায়,
ইসলামপুর
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ১৮৬১-১৯৪১ ) এক সর্বগ্রাসী প্রতিভা । পৃথিবীর খুব কম সাহিত্যেই তাঁর মত বিরল প্রতিভার উপস্থিতি চোখে পড়ে । আবার , কাজী নজরুল ইসলাম ( ১৮৯৯-১৯৭৬ ) -এর মত প্রতিবাদী কণ্ঠ পৃথিবীর সব সাহিত্যেই দুর্লভ । ' সবার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ,চেতনাতে নজরুল’ – রবীন্দ্র - নজরুল আমাদের অভিজ্ঞান । সংক্ষিপ্ত পরিসরে এদের পারস্পরিক সম্পর্কের দিকটা আলোকপাত করা যেতে পারে ।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হলে সারা বিশ্বে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে । তিনি বিশ্বকবি রূপে খ্যাত হন । বালক কাজী নজরুল ইসলাম তখন স্কুল পাঠ্য বইয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠের মাধ্যমে বিশ্বকবি '-কে খুঁজতে থাকেন ।
কাজী নজরুল ইসলাম ১৯১৭ সালে সেনাবিভাগে যোগদান করেন । সেনাবিভাগে কাজ করার সময়ে করাচিতে অবস্থান কালে তিনি রক্তের বেদন ’গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো লেখেন । সেই গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোর মধ্যে ' মেহার - নেগার ’ , ‘ স্বামী হারা ইত্যাদি গল্পে রবীন্দ্রনাথের গানের উদ্ধৃতি আছে । ধারণা করা যায় , নজরুল তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য - সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন । উল্লেখ্য , বাঙালি পল্টনে চাকরি করার সময়েই নজরুল কলকাতার বিভিন্ন পত্র - পত্রিকায় গল্প , নিবন্ধ , কবিতা ইত্যাদি প্রকাশ করতেন । ১৯২০ সালের মার্চ মাসে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হলে নজরুল স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে আসেন এবং একনিষ্ঠভাবে লেখালেখির কাজ শুরু করেন ।
১৯২১ সালের জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ও আমেরিকা সফর শেষ করে ভারতে ফিরে আসেন । সে সময় তিনি কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে অবস্থানকালে ( ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) কাজী নজরুল ইসলাম একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে যান । সম্ভবত সেটাই তাদের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ ! কাজী নজরুল সম্পর্কে খানিকটা ধারণা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগেই ছিল । তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে নজরুলকে স্বাগত জানান ।
১৯২২ সালের ৬ জানুয়ারি কাজী নজরুল ইসলামের ‘ বিদ্রোহী ' কবিতাটি বিজলী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় । কবিতাটি প্রকাশের সঙ্গেসঙ্গেই বাংলা সাহিত্যের জগতে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয় । এই কবিতাটি কাজী নজরুলকে খ্যাতির উচ্চশিখরে নিয়ে যায় । তিনি বিদ্রোহী কবি নামে বিশেষ ভাবে পরিচিত হয়ে ওঠেন । ' বিদ্রোহী ' কবিতাটি প্রকাশিত হবার কিছুদিনের মধ্যেই কাজী নজরুল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে ‘ বিশ্বকবি ’ - কে কবিতাটি পাঠ করে শোনান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন কাজী নজরুল ইসলামকে নানাভাবে উৎসাহিত করেন ।
১৯২২ সালের ২৫ জুন ' ছন্দের জাদুকর ’ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন । অকাল প্রয়াত কবির স্মরণে কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরী হলে ১১ জুলাই এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় পৌরহিত করেন স্বয়ং ‘ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । শোক সভায় কাজী নজরুল ইসলাম সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। উক্ত সভাতে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের মধ্যে আরও একবার সাক্ষাৎকার ঘটে এবং উভয়ের মধ্যে ভাবের আদান - প্রদান হয় । কাজী নজরুল ইসলাম ‘ ধূমকেতু ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা ব্যক্ত করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে সেটার জন্যে একটা ‘ আশীর্বাণী ’ প্রার্থনা করেন । রবীন্দ্রনাথ নির্দ্বিধায় ‘ ধূমকেতুর জন্যে আশীর্বাণী পাঠিয়ে দেন , যা নিম্নরূপ –
কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু ,
“ আয় চলে আয় ,রে ধূমকেতু , / আঁধারে বাঁধ
অগ্নিসেতু ,
দুর্দিনের এই
দুর্গশিরে / রাতের ভালে হোক না লেখা ,
জাগিয়ে দেরে চমক
মেরে , / আছে যারা অর্ধচেতন । ”
-
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
উল্লেখ্য , ১৯২২ সালের ১১ আগস্ট ‘ধূমকেতু পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় । এর সবকটি সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণীটি শোভা পেতো ।
১৯২২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ধূমকেতুতে কাজী নজরুলের লেখা ‘আনন্দময়র আগমনে ' কবিতাটি প্রকাশিত হয় । এই কবিতাটির জন্যে নজরুল রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হন । ১৯২২ সালের ২৩ নভেম্বর ব্রিটিশ পুলিশ নজরুলকে কুমিল্লা থেকে গ্রেফতার করে । রাজদ্রোহের অপরাধে নজরুলের এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘোষিত হয় । রায় ঘোষিত হবার পর তাকে প্রথমে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে , তারপর তাকে সাধারণ কয়েদি হিসেবে হুগলি জেলে স্থানান্তরিত করা হয় । হুগলি জেলে কয়েদিদের প্রতি খুবই দুর্ব্যবহার করা হতো এবং নিপীড়ন চালানো হতো। এরই প্রতিবাদে নজরুল এবং অন্যান্য বন্দিরা অনশন শুরু করেন । দীর্ঘদিন ধরে অনশন চললো । কাজী নজরুলের অনশনের সংবাদে বাংলার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি চঞ্চল হয়ে ওঠেন – এদের মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন । রবীন্দ্রনাথ দ্রুত নজরুলকে তারবার্তা পাঠান " " Give up hunger strike , our literature claims you " – অনশন ত্যাগ কর , আমাদের সাহিত্য তোমাকে সে দাবি জানায় ।
আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কাজী নজরুলের অবস্থান কালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তার লেখা ' বসন্ত ' গীতিনাট্যটি নজরুলের নামে উৎসর্গ করেন ( ১৯২৩ ) । এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য । ‘ জাতির জীবনে বসন্ত এনেছে নজরুল । তাই সদ্য প্রকাশিত ‘ বসন্ত ’ গীতি নাট্যখানি ওকেই উৎসর্গ করেছি এবং উৎসর্গপত্রে আমি ওঁকে ' কবি ' বলে অভিহিত করেছি । " উল্লেখ্য , কাজী নজরুল ইসলামও তাঁর ‘ সঞ্চিতা ' কাব্যখানি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেছিলেন (১৯২৮ ) ।
রবীন্দ্রযুগে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজ্ঞান কবি - সাহিত্যিক তাদের বিশিষ্টতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন কাজী নজরুল ইসলাম তাদের মধ্যে অন্যতম । তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে তার বক্তব্য - “ বিশ্বকবিকে আমি শুধু শ্রদ্ধা করে এসেছি সকল হৃদয় - মন দিয়ে ; যেমন করে ভক্ত তার ইষ্টদেবতাকে পূজা করে । ছেলেবেলা থেকে তার ছবি সামনে রেখে গন্ধ ধূপ - ফুল - চন্দন দিয়ে সকাল - সন্ধ্যা বন্দনা করেছি । তারপর কতদিন দেখা হয়েছে , আলাপ হয়েছে । নিজের লেখা দু - চারটি কবিতা - গানও শুনিয়েছি । অবশ্য কবির অনুরোধেই । আমার অতি সৌভাগ্যবশত অতি প্রশংসাও লাভ করেছি কবির কাছ থেকে । সে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় কোনও দিন এতটুকু প্রাণের জন্য বা মন - রাখা ভাল বলবার চেষ্টা দেখিনি । ” নজরুল যেমন রবীন্দ্রনাথকে ‘ গুরু ' জ্ঞানে শ্রদ্ধা - ভক্তি করতেন । রবীন্দ্রনাথও নজরুলকে তেমনি ‘ শিষ্য ’ জ্ঞানে তার স্নেহ - ভালবাসা উজাড় করে দিতেন ।
পরিশেষে বলা যায় – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে (আগস্ট , ১৯৪১ ) কাজী নজরুল ইসলাম ব্যথাভরা কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন ' গুরুদেব ’ - এর উদ্দেশ্যে “ আকাশের রবি হয়ে এসেছিলে তুমি বাংলার ঘরে / আজ তুমি চলে গেলে সকল শূন্য করে । ” কাকতালীয় ঘটনা হলেও আমাদের মনে হয় - নজরুল গুরুদেবের মৃত্যুকে সহ্য করতে পারেননি । মাত্র এক বছরের মাথায় ১৯৪২ সালে তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে বোধশক্তিহীন ও নির্বাক হয়ে পড়েন । ১৯৭৬ সালে কাজী নজরুল ইসলামের দৃশ্যমান মৃত্যু ঘটলেও ‘ বাস্তব মৃত্যু ’ কিন্তু তার ১৯৪২ সালেই ঘটে গিয়েছিল । একেই বোধহয় বলা যায় । গুরু - শিষ্যের আত্মিক টান ’ !
লেখক পরিচিতি –
ড.বাসুদেব রায়ের
জন্ম ১৯৬২ সালে। কবিতার মাধ্যমে সাহিত্যের জগতে আত্মপ্রকাশ। প্রথম প্রকাশিত বই
মানব' (কাব্যগ্রন্থ), দ্বিতীয় বই রক্তের বাঁধন (উপন্যাস)। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়
পদচারণা করলেও প্রবন্ধ সাহিত্যের দিকে তার ঝোঁক বেশি। তদুপরি গবেষণামূলক প্রবন্ধ
তথা বই লিখতে তিনি অধিকতর উৎসাহী। গবেষণামূলক বইয়ের পাশাপাশি সাধু-মহাপুরুষদের
জীবনী-গ্রন্থ, একাঙ্কিকা ইত্যাদি সম্পাদনাও করেছেন তিনি।
ড.বাসুদেব রায়ের
বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। হার উল্লেখযোগ্য গবেষণা গুলোর মধ্যে রয়েছে
মনসামঙ্গল কাব্যে দেবদেবীর স্বরূপ', চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল
কাব্যে দেবদেবীর স্বরূপ, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে
সমাজ-চিত্র ইত্যাদি। তাঁর যৌথ রচনা ও উপেক্ষণীয় নয়।
বিভিন্ন
পত্র-পত্রিকায় বাসুদেব রায় নিরলস ভাবে লিখে চলেছেন। এছাড়াও নতুন করে তিনি একক ও যৌথভাবে বেশ কয়েকটি
গবেষণামূলক কাজে হাত দিয়েছেন।